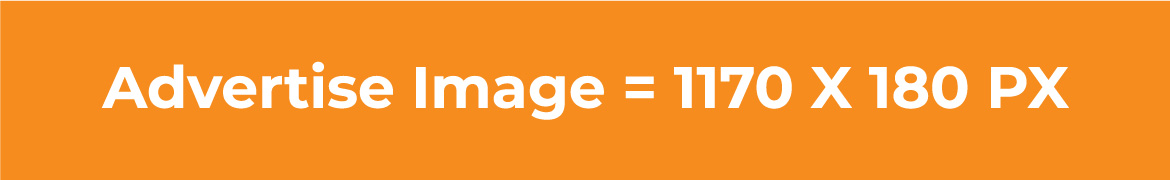example.com
Verify you are human by completing the action below.
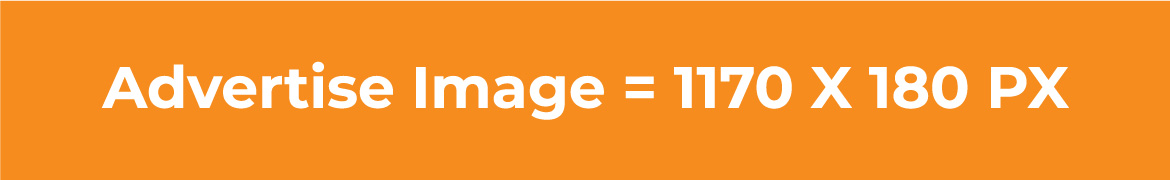
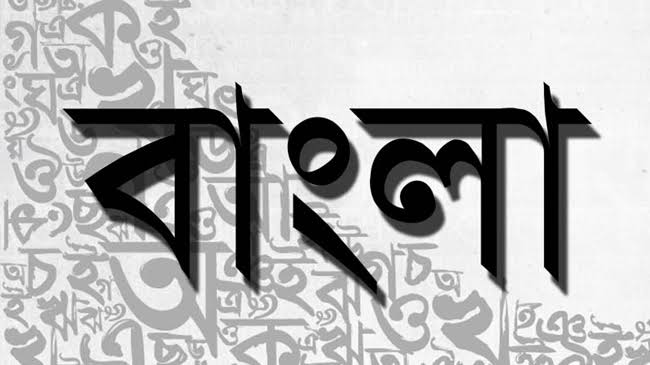
বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নির্দশন পাওয়া যাচ্ছে চর্যাপদগীতিকায়। চর্যাপদ কাব্যগুলোর ভাষা ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যকার। এসময়ের আগে বাংলা ভাষার ধ্বনি রূপ কেমন ছিল তার লিখিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিশ্চয় এই সময়ের আগেও বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল। আর্চায্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ – গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদ কাব্যগুলো উদ্ধার করেন। চর্যাপদে মোট ৪৭টি পদের কথা উল্লেখ রয়েছে। ঐ সময়ের কবিরা ছিলেন গৃহহীন বৌদ্ধ বাউল সাধক। তারা সাধনা করতেন গোপন তত্বের, সে তত্বগুলো তারা কবিতায় গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন, যেন একমাত্র সাধক ছাড়া আর কেউ বুঝতে না পারে। এই সংসার ত্যাগী কবিরা বলেন- কাহ্নপা, লুইপা, সারহপা, চাটিল্লপা, ডোম্বিপা, ঢেন্ডনপা, শান্তিপা,মহিত্তাপা,কুক্কুরীপা, তান্তীপা,দারিকপা, আজদেবপা, ভুসুকপা ও শবরপা। নিরাপত্তাজনিত কারণে এদের অধিকাংশই তাদের ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন এবং তারা নামের সঙ্গে `পা` (পদ) শব্দটি সভ্রমবাচক অর্থে ব্যবহার করতেন। এরা ছিলেন পূর্ব ভারত ও নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী। আবার কেউ কেউ পূর্ববঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, বিহার, উরিসা ও আসামের বাসিন্দাও ছিলেন।
মাত্র ১০০০ বছর আগের বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাপদগীতিকাগুলো সাধারণ বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পাঠ করে ওঠা আজকাল অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষা বলে মনে করতে গিয়ে দিধান্বিত হতে হয়। যেমন – কবি কাহৃপার লেখা ১০ নম্বর পদ “ নগর বাহিরিরে ডোম্বিতোহারি। দোই দোই জাসি বামহন নাড়িয়া।” চর্যাগীতিকার এই চরণটি বাংলাতে রুপান্তর করলে অর্থ দাড়াবে “ নগরে বাহিরে , ডোম্বি তোমার কুঁড়ে ঘর। ব্রাহ্মণ নেড়াকে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও।”
১২০০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা কোনো সাহিত্যকর্মের পরিচয় পাওয়া যায়না। তাই এইসময়কে বাংলা সাহিত্যের “ অন্ধকার যুগ” বলা হয়। তবে মধ্যযুগের শুরুতেই রচিত হয় একটি অসাধারন কাব্য, যার নাম “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন”। এ কাব্যটি যিনি রচনা করেন তার নাম বড়ু– চন্ডীদাস। ১৯০৯ সালে কাব্যটি বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে উদ্ধার করেন শ্রীবসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্ববল্লভ। কাব্যটির নায়ক নায়িকা কৃষ্ণ ও রাধা। এ কাব্যের ভাষা চর্যাপদ কাব্য থেকে বেশ আলাদা। যেমন – “ কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়িএ কালিসী নাই কুলে, কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ী গোঠ গোকুলে, আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। এ অনুবাদের অর্থ ‘কে বাঁশী বাজায় কালিণী নদীর কূলে? কে বাশি বাজায়এ গোকুল গ্রামে, আমার শরীর আকুল আমার মন ব্যাকুল’। মধ্যযুগ যে কাব্যগুলোর জন্য বিখ্যাত, সেগুলোকে বলা হয় ‘মঙ্গল কাব্য’। এই সময়কার বিখ্যাত কবিরা হলেন- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চৈতন্য, চন্ডীদাস, শাহ মুহাম্মদ সগীর, আলাওল প্রমুখ। এরা সবাই ছিলেন রাজসভার কবি।
মধ্যযুগ এক সময় শেষ হয়ে আসে। দেশে দেখা দেয় নানা বিপর্যয়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর সাহিত্যের পরিবর্তন ঘটে। সমাজে দেখা দেয় নতুন ধনিক শ্রেণি। তাদের দরকার হয় হাল্কা ও নিম্ন রুচির সাহিত্য। নগদ অর্থের বিনিময়ে এ সাহিত্য সরবরাহ করতেন এক শ্রেণির কবি তাদেরকে কলা হয় কবিয়ালা। কবিয়ালেরা কবিতা রচনা করতেন মুখে মুখে আর মঞ্চে দাড়িয়ে করতেন কবিতা যুদ্ধ। একটি মঞ্চে দাড়াতেন দু’দল কবি। তাদের একদল প্রথম অপর দলের উদ্দ্যেশ্যে পদ্যে কিছু বলতেন। তাদের বলা যখন শেষ হতো তখন অন্য দলের কবিরা আগের দলের জবাব দিতেন। এই সময়ের বিখ্যাত কবিয়াল হলেন- রাম বসু, নৃসিংহ, হরুঠাকুর, নিধুবাবু, কেষ্টা মুচি, রামানন্দ নন্দী প্রমুখ। তাদের ভাষার একটি নমুনাঃ ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাটিয়া চলিল। কিছুদূর যাইয়া মর্দ রওয়ানা হইল। অর্থ – বীর পুরুষ ঘোড়ার পিঠে চড়ে হেটে যায় আর কিছু দূর যাওয়ার পর রওনা হয়। বর্তমানে বাংলা ভাষায় এ ধরনের শব্দ ব্যবহার হয় না।
১৮০০ সালের জুলাই মাসে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম চত্বরে ব্রিটিশ আধিকারিদের ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় বাংলা ও হিন্দির মতো ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। হতবাক হওয়ার বিষয়, সে সময় কলকাতায় বাংলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া যায়নি। সে যুগের ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা বেকল সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। তারা বাংলায় শিক্ষকতা করতেন না! তারা সংস্কৃতকে দেবভাষা মনে করতেন! এমতাবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষ একাধিক ভারতীয় ভাষাবিদ শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান যাজক উইলিয়াম কেরিকে এই বিভাগে নিয়োগ করেন। অতঃপর কেরি মৃত্যঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে হেড পন্ডিত, রামমোহন বাচস্পতিকে সেকেন্ড পন্ডিত ও রামরাম বসুকে অন্যতম সহকারী পন্ডিতের পদে নিয়োগ করেন। এরপর এই পন্ডিতবর্গ বাংলা ভাষা গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং গড়ে তুলেন বাংলা গদ্য। এ গদ্য বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করে। নবযুগে আসে বৈচিত্র্য। গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উপন্যাস রচনা করেন প্যারিচাঁদ মিত্র, মহাকাব্য রচনা করেন মাইকেল মধূসূদন দত্ত। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা মতো বাংলা ভাষারও বিবতর্ন হচ্ছে প্রতিনিয়তি। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারিচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরে দুললের ভাষা সঙ্গে ২০১৬ সালে প্রকাশিত ইমদাদুল হক মিলনের নূর জাহান উপন্যাসের বিস্তর পার্থক্য। আদিযুগে বা মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ছিল একটি অবিকশিত বা অনুন্নত ভাষা। বাংলা ভাষা বলতে ছিল একগুচ্ছ আঞ্চলিক ভাষা- দেশের এক এক অঞ্চলে তার এক এক রূপ। সে রূপগুলোর মধ্যে অবশ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। ওই আঞ্চলিক ভাষা গুচ্ছে বা বাংলা ভাষার আদি ও মধ্য যুগে লেখা হয়েছে কিছু কবিতা ও কাব্য। তার বেশি কিছু হয়নি। তাই ঐ সময়ে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছে বেশ কম। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারও আদিতে খুব সীমিত ছিল। কালক্রমে নতুন শব্দ সৃষ্টি, পরিগ্রহন এবং আত্তীকরণের মাধ্যমে ভাষা সমৃদ্ধ হয়।
যে ভাষার আত্তীকরণ ক্ষমতা যত বেশি সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষা পর্যন্ত শব্দের বিবর্তন লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা অতি সহজ হতে পারে। যেমন- ঘি এ শব্দটা এখন আধুনিক বাংলা ভাষার শব্দ। প্রাচীন বাংলাতে উচ্চারণ হতো ‘ঘিঅ’ তার আগে ‘ঘত’ তারও আগে ‘ঘৃত’। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে বাংলা ভাষার শব্দগুলো বিবর্তিত হয়েছে। এছাড়াও ও ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার শব্দগুলো বাংলা ভাষায় প্রবেশ করছে। বাঙালী অভিবাসীরা ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে এক মিশ্র ভাষা ‘বাংরেজি’তে কথা বলছে। ইংরেজি ভাষার শব্দগুলোকে বাংলা ভাষার বর্ণে লেখা হচ্ছে। বাংলা ভাষাভাষী কিছু ছেলে মেয়েরা ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। আবার কিছু কিছু ছেলে মেয়েরা হিন্দি ভাষায় কথা বলতে আনন্দ অনুভব করছে। এসবের প্রভাব বাংলা ভাষার উপর পড়ার কারণে ভাষা তার সঠিক গতিপথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এছাড়াও রয়েছে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা। এই উপভাষার উচ্চারণ ধ্বনিগুলি বাংলা ভাষাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। আজ থেকে এক হাজার বছর পরে হয়তো এখন যে শব্দটি যেভাবে উচ্চারণ করছি বানান করছি এবং লিখছি সেটি সেভাবে নাও থাকতে পারে।
১৯৫২ সালে একটি রক্তাক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা রক্ষা করেছি আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা। এই মর্যাদার আন্দোলন বা সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমাদের অব্যাহ রাখতেই হবে। বাংলা ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে আজো। এ ষড়যন্ত্র ভাষা বিকৃতির। এ ষড়যন্ত্র ভাষা ব্যবহারের। এ ষড়যন্ত্র ভাষা সবর্ত্রকরণের ক্ষেত্রে। আমদের দেশের উচ্চশিক্ষিত লোকেরা প্রয়োজন ছাড়া সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার যে স্বদেশপ্রেমের ও সম্মানজনক বিষয় এ কথা ভাবেন না। তারা বাংলাকে অবহেলা করে ইংরেজি ভাষার কথা বলে নিজেকে সুশীল মনে করে। তাদের এ ধরণের হীন মানসিকতা ঘৃণার যোগ্য। শত নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখেও বাংলা ভাষা তার অস্তিত্ব হারায়নি, তার মূল কারণ তার গ্রহন শক্তি। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজি, তামিল, উর্দু, ওলন্দাজ, চীনা এমন কোনা ভাষা নেই যা থেকে বাংলা ভাষা শব্দ ও কথা আহরণ করেনি। নামাজ, রোযা, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, চেয়ার, টেবিল, খবর ইত্যাদি সব শব্দ বা কথাই বিদেশি ভাষা থেকে গৃহীত এবং এখন বাংলা কথা হিসেবেই জনমুখে প্রচলিত। নবপ্রযুক্তির অসংখ্য বিদেশি শব্দ, কথা ও নাম এখন বাংলা হয়ে গেছে। এমনকি আমাদের ভাষা আন্দোলনের নামটাও বিদেশী ভাষা থেকে গ্রহীত। তবে তা বাংলা হয়ে গেছে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করেছে।
বাংলা ভাষার তিন-চতুর্থাংশ শব্দই বিদেশি ভাষা থেকে আগত। বাংলা ভাষার শব্দগুলো সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন- দেশি, বিদেশি, তদ্ভব ও তৎসম। বলতে গেলে, দেশী শব্দের সংখ্যা মাত্র এক-চতুর্থাংশ বাদবাকি সব বিদেশি। তদ্ভব-তৎসম শব্দ শ্রেণিভুক্ত শব্দরাজি মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। তাই এগুলো বিদেশি শব্দ হলেও ভাষা বিজ্ঞানিদের মতে কৃত ঋণ শব্দ। কিন্তু অসাধারণ স্বীকরণ ক্ষমতার বলে বাংলা ভাষা বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।ভাষা মানুষের জীবনে মহান স্রষ্টার এক বিষ্ময়কর অবদান। প্রত্যেক ভাষার ব্যাবহার ও উপযোগিতার ওপর সে ভাষার টিকে থাকা, বিকশিত হওয়া ও অস্তিত্ব লাভ নির্ভর করে।
পূর্বে ইংরেজি অনুসরণ করে বাংলা ভাষা যেমন সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়েছে. তেমনি প্রচেষ্টার ফলে যদি তথ্য-প্রযুক্তিতে, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তামানে এবং ভবিষ্যতেও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও আইনের ভাষা হিসাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে তাহলেই আমাদের সরকারী কাজে, রাষ্ট্রীয় কাজে, ব্যাবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যবহারিক ভাষা হিসাবে বাংলা ব্যবাহারের বাধাগুলো দূর হবে। এছাড়া ও শিক্ষার সব পর্যায়ে তাকে মাধ্যম করে তোলার বর্তমান অসুবিধাগুলো তখন দূর হবে। সরকারের উচিত সব দপ্তরিক কাজে (বৈদেশিক বিষয়াদি ছাড়া) বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। মনে রাখা দরকার যে, ক্রমাগত ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীর যেকোন ভাষাই ব্যবহারিক ভাষা হয়ে উঠতে পারে এবং তখন তার ভিত খুব মজবুত হয়।
বাংলা ভাষার শব্দ সংখ্যা অনুমানিক এক লক্ষ্য ঊনত্রিশ হাজার। এদিক থেকে এ ভাষা পৃথীবীর অন্যতম সমৃদ্ধতম ভাষা। বাংলাদেশ সহ ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা, দক্ষিণ আসাম, উরিসা, বিহার, ঝাড়খন্ড, আন্দামান, নিকোবর রাজ্যে বসবাসরত বাঙালিদের মাতৃভাষা বাংলা। সেই হিসাবে, এ ভাষায় প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ কথা বলে। সে দিক থেকে এটি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্ততম ভাষা।
বস্তুত বাংলার নবজাগরনে ও বাংলার সাংস্কৃতিক বিবিধতাকে এক সূত্রে গ্রন্থনে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে তথা বাংলাদেশ গঠনে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
পরিশেষে বলা যেতে পারে, পূর্বে উর্দু ভাষার সম্রাজ্যবাদী অধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সাফল্যের সঙ্গে রুখে দিতে পারলেও বর্তমানে আমরা হিন্দি ভাষার অধিপত্যবাদী অগ্রাসনকে রুখে দিতে পারছি না। আমরা একটি যুদ্ধে জিতেছি, আরেকটি যুদ্ধ সামনে। তাতেও জয়ী হতে হবে। (সমাপ্ত)
লেখক : খায়রুল আকরাম খান
ব্যুরো চীফ : দেশ দর্শন
Some text
ক্যাটাগরি: Uncategorized