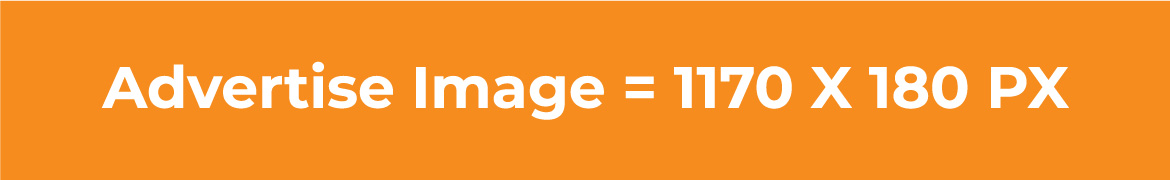গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় বিভিন্ন রকমের সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দুটি ব্যবস্থা হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ও সংসদীয় পদ্ধতি। সংসদীয় পদ্ধতিতে আবার দুটি নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো সহজ ভোটাধিক্য পদ্ধতি, অর্থাৎ ভোট প্রাপ্তির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারনের নির্বাচন, যাকে ‘ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট'(এফপিটিপি) পদ্ধতির নির্বাচন বলা হয়। এই পন্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীর মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, তিনিই নির্বাচিত হবেন। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক অর্থাৎ ‘প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেনটেশন'(পিআর) নির্বাচন বলা হয়। এই ব্যবস্থা এফপিটিপির মতো আসনভিত্তিক নয়, বরং জাতীয় ভিত্তিতে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হয়। যে দল যত ভোট পাবে, আনুপাতিক হারে সে দল ততটা সিট পাবে।
আনুপাতিক হারে নির্বাচন পদ্ধতি এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। কথিত আছে, ১৭৭৬ সালে আমেরিকান বিপ্লবের সময় দেশটির রাষ্ট্রপতি জন অ্যাডামস তার বিখ্যাত পুস্তিকা ‘থটস অন গভর্ণরমেন্ট’-এ আনুপাতিক হারে নির্বাচন পদ্ধতির প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে আধুনিক বিশ্বে সর্বপ্রথম ১৮৯৯ সালে বেলজিয়ামে পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
পিআর পদ্ধতির মধ্যে আবার তিন ধরনের নিয়ম আছে। এগুলো হলো–পার্টি-লিস্ট পিআর, মিক্সড-মেম্বার পিআর ও সিঙ্গেল ট্র্যান্সফারেবল পিআর।
জামার্নী, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে, স্পেন, গ্রিস, ইতালি, ইসরাইল, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল,শ্রীলংকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, অ্যাঙ্গোলা, ব্রাজিল, চিলি, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, নিউজল্যান্ডসহ বর্তমান বিশ্বের ১৭০ গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে ৯১ টি দেশ তাদের আইনসভার নির্বাচনে কোনো না কোনো ধরনের পিআর পদ্ধতি অনুশীলন করে। মূলত উন্নত বিশ্বে পিআর পদ্ধতির জনপ্রিয়তা বেশি।
বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, উন্নত বিশ্বে পিআর পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয় হলেও এর কিছু ইতিবাচ ও নেতিবাচক দিক রয়েছে। পিআর পদ্ধতির ইতিবাচক দিক গুলো হলো–(১)রাজনীতি হয় অন্তর্ভুক্তিমূলক; (২) এতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় ; (৩) রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহাবস্থান ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায় ; (৪) নির্বাচনে কারচুপির সুযোগ কমে আসে ; (৫) নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রণোদনা হ্রাস পায় ; (৬) সংসদ সদস্যদের গুণ ও মান বৃদ্ধি পায় ; (৭) নির্বাচনী প্রচারাভিযানের মান বৃদ্ধি পায় ; (৮) স্থানীয় সরকার বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয় ; (৯) আমলাদের পরিবর্তে রাজনৈক দলগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ; (১০) বড় দলগুলোর নিকট ছোট ছোট দলগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও মরযার্দা বৃদ্ধি পায় ; (১১) ছোট ছোট দলগুলো থেকে সংসদ সদস্য হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় ; (১২) উপ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটে ; (১৩) বৈষম্যহীন প্রতিনিধিত্বের পরিবেশ নিশ্চিত হয় ; (১৪) নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত হয় ; (১৫) সুশাসন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বৃদ্ধি ঘটে।
তবে এরকম উত্তম ও চমতকার ব্যবস্থার বিপরীতে কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে। পিআর ব্যবস্থার নেতিবাচক দিক গুলো হলো–(১)এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের অবসান ঘটে ; (২) জোটবদ্ধ সরকার সব সময় দুর্বল থাকে ; (৩) ঘন ঘন সরকারের পতন ঘটে ; (৪) ছোট ছোট দলগুলোর নিকট বড় দলগুলো জিম্মি হয়ে পড়ে ; (৫) দলের ঘাড়ে বন্দুক রেখে অধস্তনদের নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি হয় ; (৬) মনোনয়নে পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা বৃদ্ধি পায়।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, আনুপাতিব নির্বাচন ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধার দিক গুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রচুর গবেষণা করতে হবে। পাশাপাশি এই পদ্ধতি প্রবতর্নের জন্য আগে ভোটারদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে।
প্রসঙ্গগত, পিআর পদ্ধতি নিয়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে দীর্ঘদিনের মিত্র বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে বাগযুদ্ধ চলছে। তাদের নিজ নিজ দলের নেতারা টকশোগুলো মাতিয়ে রাখছেন। তারা একে অন্যকে কটাক্ষ করছেন। শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তারা মাঠে আন্দোলনে নামার হুমকি দিচ্ছেন ; কোনো কোনো দল এরই মধ্যে নেমেও পড়েছে। ফলে জনগণ দ্বিধান্বিত ও শঙ্কিত যে, কি হতে যাচ্ছে দেশে ! দ্রুত পরিবর্তন হওয়ার পরিস্থিতিতে আমাদেরও প্রশ্ন–নির্বাচন কি আদৌ সময়মতো হবে? বিএনপি কি পিআর মানবে? বিএনপি যদি না মানে, তাহলে জামায়াত ও তার সমমনা জোট কি করবে? তারা কি আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে পারবে?
বিএনপিন জন্য পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনে যাওয়া দৃশ্যত জেনেশুনে বিষ পান করার মতো। কেননা পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে বিএনপি এককভাবে কখনো ক্ষমতায় যেতে পারবে না। অতীতে ৪০ শতাংশের নিচে ভোট পেয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় গেছে। কিন্তু এবার বিএনপি সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ ভোট পেলেও তাতে পিআর পদ্ধতিতে আসন পাবে মাত্র ১২০ টি, যা সরকার গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। বিএনপিকে এক বা একাধিক দলের সঙ্গে কোয়ালিশন করতে হবে। আবার বিদ্যমান পদ্ধতিতে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েও বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার সম্ভবনা আছে।
অন্যদিকে পিআর জামায়াতের জন্য আবির্ভূত হবে আশীর্বাদ হিসেবে। জামায়াত ১৯৯১ সালে এককভাবে নির্বাচন করে ১২ দশমিক ১ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পেয়েছিল১৮ টি। তবে পিআর পদ্ধতি থাকলে আসন সংখ্যা হতো ৩৬ টি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর জামায়াতের সমর্থন ও ভোট নিঃসন্দেহে বেড়েছে। কত বেড়েছে বা বাড়তে পারে, তা দেখার জন্য আগামী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ডাকসু ও জাকসু নির্বাচনের ফলাফলের ট্রেন্ড কিছুটা সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত দেয়। জামায়াত জাতীয়ভাবে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভোট পেলে পিআরে তাদের আসনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬০ থেকে ৭৫ টি। বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভোট পেয়ে বিপুলসংখ্য আসনে অল্প ভোটের ব্যবধানে হারতে হতে পারে।
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন করার জামায়াতের দাবি নিয়ে চরমোনাইর পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ তাদের সমমনা জোট মাঠে আন্দোলনে নেমেছে। জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতারা মাঠে-ময়দানে গরম গরম বক্তৃতা দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের এই অবস্থান কি ধরে রাখতে পারবে? ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সঙ্গে জামায়াতের কি ঐক্য থাকবে? জামায়াত ও তার সমমনা জোট আন্দোলন করে কি দাবি আদায় করতে পারবে? তবে বিএনপি কোনোভাবেই তা মানবে না, অপরদিকে জামায়াত ও তার সমমনা জোট আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে চায়। সমাধান হবে তাহলে কিভাবে? নির্বাচন কি সময়মতো হবে? এসব উত্তর পেতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।
বাংলাদেশের ৫৪ বছরের ইতিহাসে পিআর পদ্ধতিতে কখনো কোনো নির্বাচন হয়নি। কোনো কিছু না হলেই যে ভবিষ্যতে কখনোই তা হতে পারবে না, ব্যাপারটি তেমন নয়। তবে নতুন যেকোনো পদ্ধতিরই বাস্তবতা ও উপযুক্ততা যাচাই-বাছাই করা দরকার। বলাবাহুল্য যে, একসময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কথা মানুষ কখনো জানতো না। নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবিতে ১৯৯০ সালের তুমুল গণ-আন্দোলনের সময় সময়ও এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী খালেদা জিয়া পর্যন্ত বলেছিলেন, ‘পাগল ও শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নন।’ ইতিহাস সাক্ষী, এই তত্ত্ববধায়ক সরকার ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো ও প্রয়োজনীয় ছিল বাংলাদেশে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই একাধিক সুষ্ঠু ও গ্রহনণযোগ্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে। কিন্তু পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার আদালতের রায়ের নামে ২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাসের মাধ্যমে এই তত্ত্ববধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে, যার পরিণতি ছিল ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং তাদের দেশ ছেড়ে পলায়ন।
বর্তমানে পিআর নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে দিন দিনই জটিলতা তৈরি হচ্ছে। বিএনপি পিআর মানবে বলে মনে হয় না। তারা চায় নিম্নকক্ষে প্রাপ্ত সিটের আনুপাতিক হারে(সংরক্ষিত মহিলা আসনের মতো) উচ্চকক্ষের আসন বণ্টন করা হোক। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল জামায়াত ও তাদের সমমনা জোটের অবস্থান বিএনপির পুরো উল্টো। পিআর নিয়ে তারা মাঠে আন্দোলনে নেমেছে। ঐক্যমত্য কমিশনের সমঝোতা বৈঠক চলা অবস্থায় আন্দোলনে-যাওয়ায় তাদের কঠোর সমালোচনা করছে বিএনপি এবং তারাও মাঠে নামার হুমকি দিচ্ছে।
এভাবে পারস্পারিকভাবে দোষরোপ করতে থাকলে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মাঠে নামলে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দুর্বল সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি সামলানো কঠিন হয়ে যাবে। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেলে তখন তা সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এ অবস্থায় জরুরি অবস্থা জারিসহ ১/১১ সরকারের মতো কোনো সরকার জাতির ঘাড়ে চেপে বসতে পারে–এ ধরনের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন রাজনীতিবিদদের আর কিছুই করার থাকবে না।
সুতরাং পিআর নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা কয়েকভাবে সমাধান করা যেতে পারে। প্রথমত, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে সকল রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নেবে–উভয় কক্ষের নির্বাচন বিদ্যমান ‘এফপিটিপি ‘পদ্ধতিতে হবে, নাকি পিআরের মাধ্যমে হবে। দুটোই বিশ্বের স্বীকৃত পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত, সব দল যদি ঐক্যমত্যে পৌঁছতে না পারে, তবে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিবে–নিম্নকক্ষের সদস্যগন বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবে, আর উচ্চকক্ষ নির্বাচিত হবে পিআরের মাধ্যমে। তৃতীয়ত,আলোচিত দুটি প্রস্তাবের কোনোটিতেই যদি মতৈক্য না হয়, তাহলে ৫০ শতাংশ হবে বিদ্যমান এফপিটিপি পদ্ধতিতে, আর ৫০ শতাংশ হবে পিআর পদ্ধতিতে। চতুর্থত, প্রস্তাবিত ও আলোচিত পদ্ধতির কোনোটিতেই যদি সমঝোতা বা ঐক্যমত্য না হয়, তাহলে পুরো ব্যাপারটি জনগণের কাছে ছেড়ে দেওয়া, অর্থাৎ ‘ গণভোট ‘ আয়োজন করা যেতে পারে। অতএব, জনগণকেই যথার্থ সিদ্ধন্ত নিতে দিন। জনগণ ভোটের মাধ্যমে যা জানাবে বা যে সিদ্ধান্ত ও মতামত দিবে, তা সবাইকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কারণ, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক।
খায়রুল আকরাম খান
ব্যুরো চীফ : deshdorshon.com
Some text
ক্যাটাগরি: Uncategorized